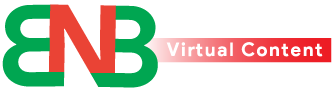যক্ষ্মা সাধারণত বায়ুবাহিত রোগ, যা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। একজনের হয়তো টিবির জীবাণু রয়েছে, পালমোনারি টিউবার কোলোসিস যাকে বলা হয়, প্রতিবার হাঁচি বা কাশির সঙ্গে সাড়ে তিন হাজার ড্রপলেট বের হয়, যা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। বাতাসের সঙ্গে ভেসে বেড়ানো ড্রপলেট নাক দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে—এমন যে কারও যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। যক্ষ্মার জীবাণু যে কেবল ফুসফুসকে আক্রান্ত করে তা নয়; এটি মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে, ত্বক, অন্ত্র, লিভার, কিডনি, হাড়সহ দেহের যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সংক্রমিত হতে পারে। টিকা বা ভ্যাকসিনেশনের মধ্য দিয়ে যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা যায়। জেনে নিই যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার।

যক্ষ্মার বর্তমান পরিস্থিতি
বিশ্বের ১০টি মৃত্যুর কারণের মধ্যে অন্যতম যক্ষ্মা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) তথ্যে, প্রতিদিন যক্ষ্মায় বিশ্বে চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং আক্রান্ত হন ৩০ হাজার মানুষ। আর জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে যক্ষ্মার উপসর্গ আছে এমন প্রায় ২৯ লাখ মানুষের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতে নতুন করে ২ লাখ ৬২ হাজার ৭৩১ জন যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত করা হয়।
যক্ষ্মা নির্ণয়ে সময়সীমা
যক্ষ্মা রোগের জীবাণু টিউবার কোলোসিসের ব্যাকটেরিয়া নির্ণয়ের জন্য সময় লাগে ছয় থেকে আট সপ্তাহ। অথচ অন্য ব্যাকটেরিয়া তিন দিনের ভেতর কালচার করা যায়। আমাদের দেশে টিউবার কোলোসিসের জীবাণু খুবই ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর ২২টি দেশে টিউবার কোলোসিসের রোগী খুব বেশি পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় চীন অথবা ভারতে। আমাদের অবস্থান এর আগেও ছিল ষষ্ঠ। বর্তমানে সপ্তম।
যক্ষ্মা সংক্রমণ ঝুঁকিতে কারা
যক্ষ্মা হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসায় কাজ করছেন এমন মানুষের যক্ষ্মা রোগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আবার যারা বস্তিতে থাকেন; যারা গরিব, অপুষ্টির শিকার, ডায়াবেটিসের রোগী; যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন যে কেউ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারেন।
যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ
ফুসফুসের টিবির লক্ষণ দুই রকম। একটি জেনারেল, অন্যটি সিস্টেমিক। জেনারেল লক্ষণের মধ্যে খাওয়ার রুচি কমে যাওয়া, দুর্বল লাগা ও শরীর খুব ঘামা। আর বিশেষ লক্ষণের মধ্যে কাশি হওয়া, কফ বের হওয়া, কফের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও বুক ব্যথা হতে পারে।
যক্ষ্মা রোগের পরীক্ষা
দুই বা তিন সপ্তাহের কাশি হলো, অ্যান্টিবায়োটিকে যাচ্ছে না, তখনই রোগীর টিউবার কোলোসিস হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। যক্ষ্মার কিছু সাধারণ পরীক্ষা আছে। যক্ষ্মা নির্ণয়ে সাধারণত এমটি টেস্ট, স্পুটাম টেস্ট, স্মিয়ার টেস্ট, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, কালচার টেস্ট, এফএনএসি ও বর্তমান যুগের সবচেয়ে আধুনিক জিন এক্সপার্ট পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। রোগের ধরন বুঝে নমুনা হিসেবে রোগীর কফ, লালা, হাড়, বা গ্লান্ডের তরল সংগ্রহ করা হয়।
কারা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন যক্ষ্মা রোগের?
দেশের মোট জনসংখ্যার একটি অংশ জন্মগতভাবেই যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বহন করে। তবে শরীরে জীবাণু থাকা মানেই এই নয় যে ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত। তবে জীবাণুর ধারক নিজে আক্রান্ত না হলেও তার মাধ্যমে অন্যের শরীরে যক্ষ্মা ছড়াতে পারে। আর সেটা যে কোনো অঙ্গেই হতে পারে। এই জীবাণু থেকে তাদেরই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। ডায়াবেটিসের রোগীদের এই জীবাণুতে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি। এ ছাড়া পরিবেশদূষণ, দরিদ্রতা, মাদকের আসক্তি, অপুষ্টি, যক্ষ্মার হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
ফুসফুস ছাড়াও শরীরের যেসব অঙ্গে যক্ষ্মা সংক্রমিত হয়
ফুসফুসে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমিত হলে টানা কয়েক সপ্তাহ কাশি, কফের সঙ্গে রক্ত যাওয়ার মতো সাধারণ কিছু লক্ষণের ব্যাপারে কমবেশি প্রায় সবারই জানা। শরীরের যে অংশে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমিত হবে, সেই অংশটি ফুলে উঠবে। যেমন গলার গ্লান্ড আক্রান্ত হলে গলা ফুলবে, মেরুদণ্ডে আক্রান্ত হলে পুরো মেরুদণ্ড ফুলে উঠবে। ফোলা অংশটি খুব শক্ত বা একদম পানি পানি হবে না। সেমি সলিড হবে। ফোলার আকার বেশি হলে ব্যথাও হতে পারে। লিভারে যক্ষ্মা হলে পানি এসে পেট অস্বাভাবিক ফুলে যেতে পারে। মস্তিষ্কে সংক্রমিত হলে সেখানেও পানির মাত্রা বেড়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের মস্তিষ্ক যে ইডিমা বা পানির মধ্যে থাকে, সেটার পরিমাণ বেড়ে যায়। চামড়ায় বা অন্য যেখানেই হোক না কেন, সেই অংশটা ফুলে ওঠে। এ ছাড়া ক্ষুধামান্দ্য, হঠাৎ শরীরের ওজন কমে যাওয়া, জ্বর জ্বর অনুভব হওয়া, অনেক ঘাম হওয়া ইত্যাদি যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ।
যক্ষ্মা রোগের করণীয় কী
যদি শরীরের কোনো অংশ ফুলে ওঠে আর কয়েক দিনেও ফোলা না কমে, এ ছাড়া ফুসফুসে যক্ষ্মার লক্ষণগুলোর মধ্যে হাঁচি-কাশি বাদে বাকি লক্ষণগুলোর কোনো একটি দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে যে ব্যক্তি যক্ষ্মায় আক্রান্ত কিনা। সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে যক্ষ্মা পুরোপুরি সেরে যায়, তাই দেরি না করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
যক্ষ্মা দীর্ঘমেয়াদি রোগ হওয়ায় এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ খেতে হয়। যেটা ৬ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় যক্ষ্মা রোগীদের ধৈর্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী পুরো মেয়াদে ওষুধ খেতে হবে। তবে অনেক সময় দুই থেকে তিন মাস ওষুধ খাওয়ার পর রোগী খুব ভালো অনুভব করে। তার রোগের সব লক্ষণ চলে যায়। এমন অবস্থায় অনেকেই সেরে উঠেছেন ভেবে ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেন। এ ক্ষেত্রে পরে আবারও যক্ষ্মা হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তার ক্ষেত্রে আগের ওষুধ কোনো কাজে আসে না।
এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। সঠিক সময় চিকিৎসা না নিলে এই জীবাণু শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে এবং চিকিৎসা না নেওয়ার কারণে তার মাধ্যমে আরও অনেকের মধ্যে জীবাণুটি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।
শরীরের অন্য অংশের যক্ষ্মা কতটা ছোঁয়াচে
যত যক্ষ্মা রয়েছে, এর মধ্যে ৮০ ভাগই ফুসফুসে হয়ে থাকে এবং এটি সবচেয়ে গুরুতর ও ভীষণ ছোঁয়াচে। ফুসফুসের যক্ষ্মা আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে সুস্থ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে। মূলত হাঁচি-কাশির মাধ্যমে, এমনকি কথা বলা থেকেও যক্ষ্মার জীবাণু খুব দ্রুত একজনের কাছ থেকে আরেকজনের ভেতর ছড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যক্ষ্মা এতটা ছোঁয়াচে নয়। তাই এটি ফুসফুসে যক্ষ্মার মতো ঝুঁকিপূর্ণ নয়। শুধু আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার আক্রান্ত স্থান সুস্থ ব্যক্তির কাটা অংশ স্পর্শ করেন, তাহলে এই রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে।
যক্ষ্মা ছড়ানো প্রতিরোধের উপায়
যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ানো প্রতিরোধে হাঁচি-কাশির সময় মুখে রুমাল দেওয়া, না হলে অন্তত হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বা সবার থেকে দূরে গিয়ে কাশি দেওয়া। যেখানে সেখানে থুতু-কফ না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে ভালোভাবে জায়গাটি পরিষ্কার করা বা মাটিচাপা দেয়া। কারও মুখের সামনে গিয়ে কথা না বলা অথবা যক্ষ্মা জীবাণুমুক্ত রোগীর সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলা।
যক্ষ্মা রোগীর আক্রান্ত স্থান, সুস্থ ব্যক্তির ক্ষতস্থানের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা। পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। রোগী জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
https://bangla-bnb.saturnwp.link/health-tips-for-mother/
থ্রিএইচটি প্রতিরোধক থেরাপির মাধ্যমে এই জীবাণু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে রিফাপেন্টিং নামে একটি ওষুধ প্রতি মাসে একবার করে তিন মাস খেতে হয়।